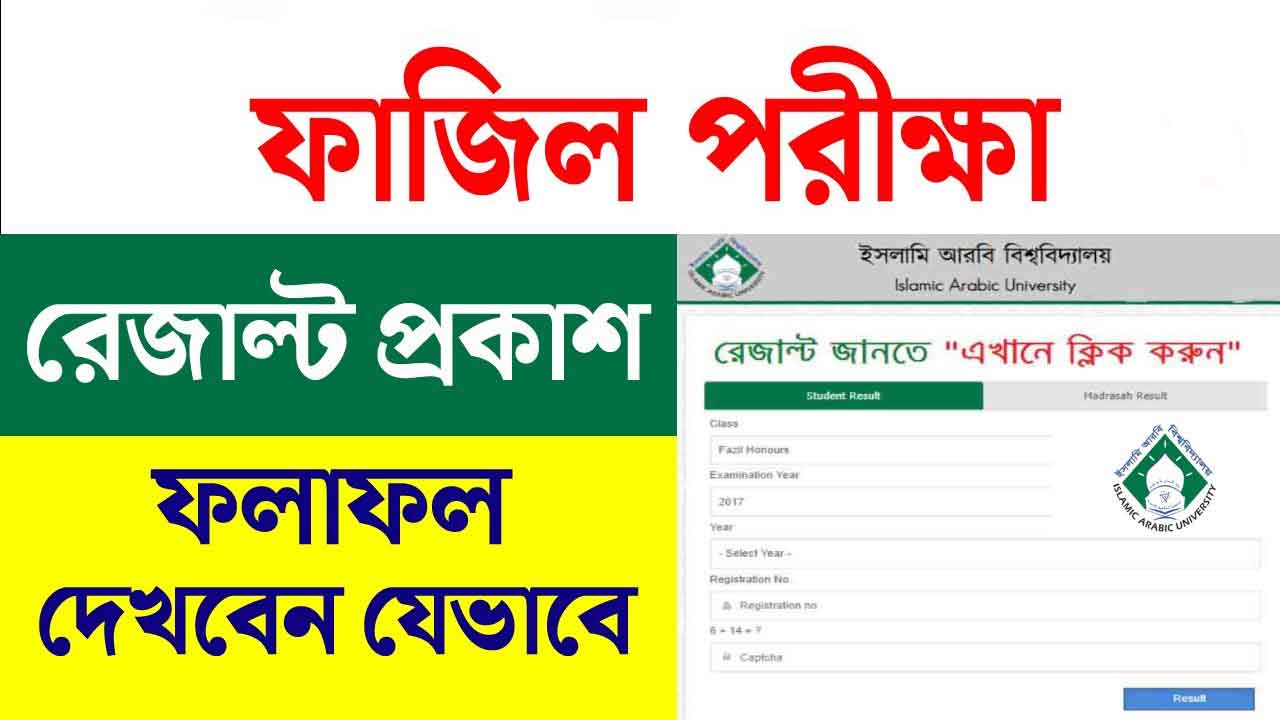বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্রের শেষদিনকে চৈত্র সংক্রান্তি হিসেবে পালন করা হয়। পুরাণমতে, এ দিনের নামকরণ করা হয়েছিল ‘চিত্রা’ নক্ষত্রের নামানুসারে। আদিগ্রন্থ পুরাণে বর্ণিত আছে, সাতাশটি নক্ষত্র; যা রাজা প্রজাপতি দক্ষের সুন্দরীকন্যার নামানুসারে নামকরণ করা হয়।
সে সময় প্রবাদতুল্য সুন্দরী এ কন্যাদের বিয়ে দেওয়ার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত রাজা দক্ষ। উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে লাগলেন তিনি। বহুদিন খুঁজেও কন্যাদের যোগ্য পাত্র পাচ্ছিলেন না প্রজাপতি দক্ষ। শেষমেষ একদিন মহা ধুমধামে চন্দ্রদেবের সঙ্গে বিয়ে হলো দক্ষের সাতাশ কন্যার। দক্ষের এক কন্যা চিত্রার নামানুসারে চিত্রা নক্ষত্র এবং চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্র মাসের নামকরণ করা হয়। রাজা দক্ষের আরেক অনন্য সুন্দরী কন্যা বিশখার নামানুসারে ‘বিশাখা’ নক্ষত্র এবং ‘বিশাখা’ নক্ষত্রের নামানুসারে বৈশাখ মাসের নামকরণ করা হয়।
বাঙালি ঐতিহ্যে দিনটি পালন করা হয় নানা উৎসব আয়োজনে। মূলত খাজনা পরিশোধের দিনটিকে পরবর্তীতে উৎসবের দিন ধার্য করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালিরা গাজন, নীল পূজা বা চড়ক পূজা পালন করেন। এ ছাড়াও চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ও শেষ প্রস্তুতি চলে হালখাতার। আদিবাসী সম্প্রদায় পালন করে বর্ষবিদায়, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বৈসাবি। যে চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে বাঙালির এত আয়োজন সেই চৈত্রের রয়েছে এক মর্মান্তিক ইতিহাস।
চৈত্র্যের শেষ দিনে জমিদার বাড়ির উঠানে আয়োজন করা হতো কবিগান, লাঠিখেলা ও হরিনাম সংকীর্তনের। যা কৃষিদেবতা হিসেবে লোকপালের লৌকিক খ্যাত। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মূল শিবের গাজনের সঙ্গে এর কোনো মিলই ছিল না। প্রজাদের আকৃষ্ট করতেই এসব আয়োজন করা হতো।
কারণ এ সময় সব প্রজার আসতেই হতো এখানে খাজনা দিতে। জমিদার বাড়ি থেকে আগেই ঘোষণা করা হতো যে, সালতামামির খাজনা সবটুকু শোধ করলে আলাদা করে কোনো সুদ লাগবে না। তাই দলে দলে মানুষ সেখানে উপস্থিত হতো। এ সুযোগে জমিদাররা একদিনে পুরো বছরের খাজনা আদায় করে ফেলতেন। অন্যদিকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রজাদেরও দর্শন দিতেন বছরের ওই একটি দিনই।
তবে কতজন প্রজা দিতে পারতেন পুরো খাজনা। বেশিরভাগ প্রজা পুরোটা তো দূরে থাক অর্ধেক খাজনাও পরিশোধ করতে পারতেন না। তাদের কপালে ছিল ভয়াবহ শাস্তি। বাংলায় শুধু ব্রিটিশরাই শাসন আর শোষণ করেনি। পরবর্তীতে বাঙালি জমিদাররাও যেন ব্রিটিশদের ওই গুণ ধারণ করেছিলেন মনে-প্রাণে। সেই শাস্তিও ছিল ভয়ানক কঠিন।
ঋণে জর্জরিত কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে চৈত্রের শেষ দিনে বড়শিতে বেঁধে চড়কে ঘোরানো হতো। যাকে এখন চড়ক পূজাও বলা হয়। লেখক আখতার উল আলম পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে পেয়েছিলেন এ নিষ্ঠুরতার বর্ণনাগুলো। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বরিশালের জমিদাররা তার মধ্যে অন্যতম। যদিও চড়ক সংক্রান্তিতে বড়শি ফোঁড়া বা বাণ ফোঁড়া ছিল প্রথমে অপেক্ষাকৃত নীচু সম্প্রদায়ের প্রথা। ব্রাহ্মণরা এতে অংশগ্রহণ করতেন না।
কিন্তু খাজনা আদায় করতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাস হওয়ার পর জমিদাররা এ প্রথা বাজেভাবে ব্যবহার করেন। ১৮০০ সালের দিকে শুরু হওয়া এ ভয়ানক শাস্তির প্রথা চলেছিল শতাব্দীর শেষ নাগাদ। ১৮৯০ সালের পর থেকে এ শাস্তি বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৮৬৫ সালের দিকে ইংরেজরা এমন নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে চেয়েছিল। তবে তা সম্ভব হয়নি।
যদিও জনশ্রুতি আছে, বাংলায় এটা শুরু হয়েছিল ১৪৮৫ সালে, রাজা সুন্দরানন্দ ঠাকুরের আমলে। তখন তাদের রাজপরিবারেই এটি পালন করা হতো। পরে তা ছড়িয়ে যায় পূর্ববঙ্গের সব প্রদেশে। মহা ধুমধামে চৈত্রের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী চড়ক পূজার উৎসব চলতে থাকে।
এমনিতেই চৈত্র মাস রুক্ষ্ম শুষ্ক মাস। এ সময় মানুষের বিশেষ কোনো কাজ থাকে না। মাঠ-ঘাট পানির অভাবে ফেটে চৌচির। সেখানে ফসল ফলানো অসম্ভব ছিল। আবার সারাবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগ ছিল বাংলার সঙ্গী। তিন বেলা খাওয়ার মতো ফসল থাকত না ঘরে। সেখানে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করা ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে চেপে বসত কৃষকের পিঠে।
কিন্তু জমিদাররা প্রজাদের খাজনা জমা দেওয়ার শেষ দিন স্থির করেছিলেন সেই চৈত্রের ৩০ তারিখ। খাজনা দেওয়ার ভয়ে বহু প্রান্তিক কৃষক বাধ্য হতেন আত্মহত্যা করতে। এটা ছিল জমিদার-মহাজন ও ব্যবসায়ীর সম্মিলিত ফাঁদ, যেখানে প্রতিটি মানুষ পা দিতে বাধ্য হতো। অভাবের তাড়নায় হোক বা নিত্যপ্রয়োজনে, দায়ে পড়ে এ তিন শ্রেণির কাছে যেত এবং সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে ফিরত তারা। প্রয়োজনে মহাজনরা পাইক পাঠিয়ে আদায় করতেন তাদের সমস্ত সুদ-আসল।
আর যাদের এত সুদের বোঝা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তারা খাজনা দিতেও পারতেন না। সেই সব প্রজাদের জন্য ছিল জমিদারের বিশেষ ব্যবস্থা। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে লেঠেল দল তৈরি করতেন। সেই দলের ভয়ে ‘বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত’। সেই লেঠেল দল গোটা জমিদারি এলাকায় প্রজাদের শাসিয়ে বেড়াত। পাশাপাশি প্রায়ই ৩০ চৈত্রের মধ্যে পুরো খাজনা জমা দিতে বাধ্য করত।
না পারলে পাইক-লেঠেলদের হাতে বন্দি হয়ে মোটা বড়শির সুঁচালো ফলায় গিয়ে ঝুলে পড়া। চড়কের পুরো বিকেলে রক্তাক্ত পিঠে চিৎকার করতে করতে, জমিদার আর সাধারণ মানুষকে কষ্টের অভিনয় করে দেখানো।
এ দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। তাদের পরোক্ষভাবে যেন এটাই বোঝানো হতো, খাজনা দেওয়া বাকি থাকলে তাদের অবস্থাও এ রকম হবে। এতে খুশি হয়ে জমিদাররা পাঁঠা বলি দিতেন, মেলার আয়োজন করতেন, আড়ং বসাতেন। সমগ্র অংশে জমিদারদের গলায় গলা মিলিয়ে সাহায্য করতেন সাহাশুঁড়ি, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা।
চড়ক পেরিয়ে গেলেও সাধারণ মানুষ, কৃষক শ্রেণির কেউই বৈশাখী নববর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারতেন না। কারণ চৈত্রের শেষ দিনের সেই ভয়াবহ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিত। পরের বছরের সেই দিনটির জন্য অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু হতো সেই নির্ঘুম রাতেই। পরের বছরও যখন সাধারণ কৃষক খাজনা দিতে পারবেন না; তখন একই শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ততদিনে এবছরের ক্ষত শুকাতে থাকুক।
এ জন্য নববর্ষকে তৎকালীন সময়ে অনেকেই ব্যঙ্গের চোখে দেখতেন। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি তার 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘কয়েক বৎসর হইতে পূর্ববঙ্গে ও কলিকাতার কেহ কেহ পয়লা বৈশাখ নববর্ষোৎসবের করিতেছে। তাহারা ভুলিতেছে বিজয়া দশমীই আমাদের নববর্ষারম্ভ। বৎসর দুটি নববর্ষোৎসব হইতে পারে না। পয়লা বৈশাখ বণিকরা নূতন খাতা করে। তাহারা ক্রেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধার আদায় করে। ইহার সহিত সমাজের কোনো সম্পর্ক নাই। নববর্ষ প্রবেশের নববস্ত্র পরিধানদির একটা লক্ষণও নাই।’
যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির মতে, বিজয়া দশমীই আমাদের নববর্ষ। আবার অনেকের মতে, অঘ্রাণ মাসই নববর্ষের মাস। কিন্তু কোনোভাবেই বৈশাখী নববর্ষ আমাদের আদি নববর্ষের সূচনালগ্ন ছিল না। তবে নববর্ষের সূচনা সেকালে খুব সুখকর ছিল না বাঙালির জীবনে।
চৈত্র সংক্রান্তির মর্মান্তিক ইতিহাস : ঋণগ্রস্ত চাষিদের নির্মমভাবে ঝুলিয়ে ঘোরানো হতো
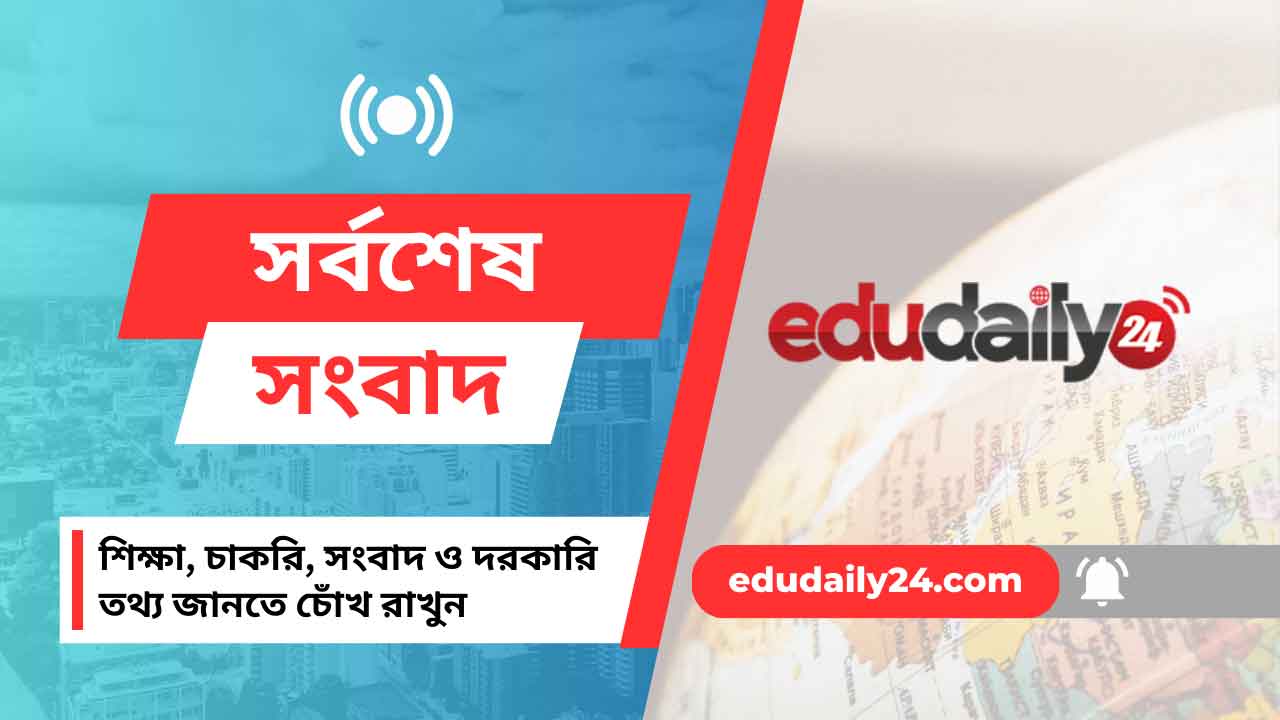
Connect With Us:
Advertisement
Our Editorial Standards
We are committed to providing accurate, well-researched, and trustworthy content.
Fact-Checked
This article has been thoroughly fact-checked by our editorial team.
Expert Review
Reviewed by subject matter experts for accuracy and completeness.
Regularly Updated
We regularly update our content to ensure it remains current.
Unbiased Coverage
We strive to present balanced information.



![রমজান মাসের সেহরি ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ [ঢাকা ও ৬৪ জেলার সময়]](https://edudaily24.com/uploads/2025/09/ramadan-timing.jpg)